জানুয়ারী, ১৯৯৯
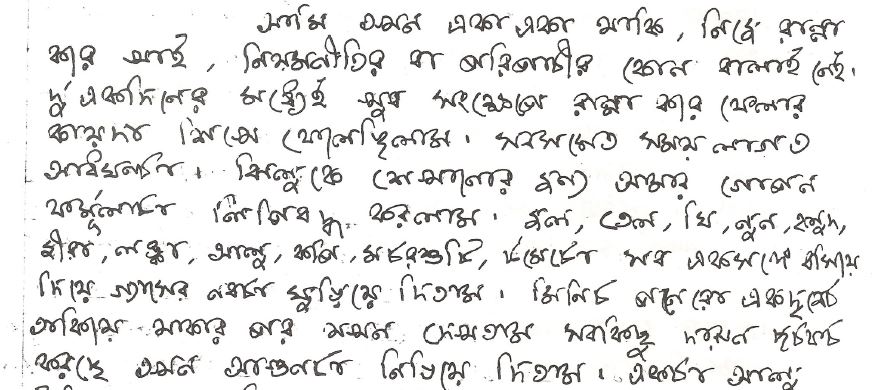
আমি তখন একা একা থাকি, নিজে রান্না করে খাই, নিয়মনীতির বা পরিপাটীর কোন বালাই নেই। দু-একদিনের মধ্যেই খুব সংক্ষেপে রান্না করে ফেলার কায়দা শিখে ফেলেছিলাম। সবসমেত সময় লাগত আধঘন্টা। ঝিলুকে শেখানোর জন্য আমার গোপন ফর্মুলাটা লিপিবদ্ধ করলাম। জল, তেল, ঘি, নুন, হলুদ, জীরা, লঙ্কা, আলু, কপি, মটরশুঁটি, টমেটো সব একসঙ্গে বসিয়ে দিয়ে, গ্যাসের নব্টা ঘুরিয়ে দিতাম। মিনিট পনেরো একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর যখন দেখতাম সবকিছু দারুন ছটফট করছে, তখন আগুনটা নিভিয়ে দিতাম। একটা আলু উঠিয়ে চামচ দিয়ে চাপ দিয়ে দেখে নিতাম পুরোপুরি নরম হয়েছে কিনা। ব্যাস! এরপর ভাত। এরজন্য আলাদা কুকার আছে। এককৌটো চাল আর দেড় কৌটো জল, একবার শুধু স্যুইচটা টিপে দিলেই আর কোন হিসেব রাখার দরকার হবে না। রান্না শেষ! যখন খুব ক্ষিদে পেত তখন একটু খেয়ে নিতাম। একবার রান্না করলে তিনদিন আরাম। তখন ভাবতাম কিভাবে লোক এই খাওয়া-দাওয়ার পিছনে প্রায় সমস্ত সময় কাটায়। অবশ্য অন্যকে দোষ দিয়ে কি হবে আমার সময় যে কিভাবে কাটতো তা আমি নিজেই জানতাম না। নিজে নিজে রান্না করে খাওয়ার এই দুর্লভ সুযোগ আমার জীবনে আসার কারণ ছিল শিল্পা, সুমেধা ও লক্ষ্মীর অনুপস্থিতি। ওঁরা সবাই গরমের ছুটি কাটাচ্ছিল সুইজারল্যান্ডে ইউজী কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে। আর আমি দিনগত পাপক্ষয় করতাম ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির নব ঘুরিয়ে, কম্পিউটারের মনিটারের দিকে তাকিয়ে, নয়ত কাগজের উপর কলমের হিজিবিজি কেটে। আমার কাছে এসব কাজের অবশ্য কোনো মূল্যই ছিলনা। জীবনের সেই সময় এক রাতে সিনেমা দেখার মত পরিষ্কার এই স্বপ্নটা দেখেছিলাম – তাহলে শোন্ এবার স্বপ্নটা আর হাল্কা মনে প্রাণ খুলে হেসে যা।
আমি অজানা এক নদীর পাড় ধরে একা একা হেঁটে চলেছি। নদীটা খুব বড় নয় আবার ছোটোও নয়, ওপাড় মোটামুটি দেখা যায়। কিছুক্ষণ হাঁটার পর একটা পুরোনো রাজপ্রাসাদ চোখে পড়ল। একটু কাছ থেকে দেখার ইচ্ছা হ’ল, তাই পায়ে পায়ে প্রাসাদের চত্বরে এসে হাজির হলাম।বারান্দায় দেখলাম কিছু অল্পবয়সের ছেলেমেয়েরা কোনো একটা বিষয়ে গম্ভীরভাবে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। বুঝলাম, আমি ভারতবর্ষেরই কোনো এক জায়গায় অজান্তে এসে হাজির হয়েছি এবং এঁদের কাউকেই আমি চিনি না। সবাই হয়ত এখানে ভ্রমণে এসেছে। যাই হোক সেসব নিয়ে কোনরকম কৌতূহল না দেখিয়ে, আমি একটা বেঞ্চে বসে নদীর উপর দিয়ে যাওয়া নৌকাগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। হয়ত আপনমনেই কিছু বলছিলাম, জানিনা এক মহিলার কন্ঠস্বরে ধ্যান ভাঙ্গল। মুখ ঘুড়িয়ে তাকাতেই জিজ্ঞাসা করল, কার সঙ্গে কথা বলছিলাম এবং আমার কথাবার্তা তাঁদের বোধগম্য হচ্ছে না।
– “কই আমি কাউকে কিছু বলেছি বলে তো আমার কিছু মনে পড়ছে না”।
– এই যে বললেন, আমি সত্য, তুমি সত্য, জগৎ সত্য।
– তা ঠিক, কিন্তু এ সম্পর্কে আমাদের সব অভিজ্ঞতা মিথ্যা। আমি আমার সম্পর্কে, আপনাদের সম্পর্কে, জগৎ সম্পর্কে যা জানি বা বুঝি সব আপেক্ষিক, পরিবর্তনশীল। আর সত্য যদি ধ্রুব হয় তাহলে এ সমস্ত কিছুই মিথ্যা।
– বেদান্ত বলে জগৎ মায়া শুধু ব্রহ্ম সত্য।
– এ সমস্ত ধারণা মানুষের চিন্তার পরিণতি। চিন্তার বিকাশ ঘটেছিল একক থেকে বিভাজনের প্রক্রিয়ার দ্বারা। অখন্ডে চিন্তা লীন। কোন প্রকাশ থাকে না। শব্দ যেমন মাধ্যম ছাড়া জন্মাতে পারে না, সেরকম চিন্তাও মানুষের মন ছাড়া প্রকাশ পায় না। শব্দের মতনই চিন্তার মধ্যেও মাধ্যমের গুণ ও প্রকৃতি জড়িয়ে থাকে।বিশুদ্ধ চিন্তা বলে কিছু নেই। মানবজাতির সমস্ত জ্ঞান চিন্তালব্ধ। ব্যাক্তিগত ভাবনা ছাড়া কোন জ্ঞান রূপ ধারণ করতে পারে না।
– তাহলে পরম সত্য বলতে কি কিছু নেই?
– সেটা জানার কোনো উপায় নেই।
– কেন?
– সত্যকে জানার জন্য আমরা যার উপযোগ করি, তার সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় সত্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, আমরা যখন কোন জিনিসকে দেখি, তখন দেখামাত্রই যা দেখছি তার ততক্ষণে গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেছে।
– মনে হচ্ছে আপনি আমাদের আশাহীন অবস্থার মধ্যে এনে ছেড়ে দিচ্ছেন! আচ্ছা, আমাদের প্রাচীন ঋষিরা বলতেন –“পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে”। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?
– পূর্ণ-র জায়গায় শূণ্য করে দিলে চলে যেতে পারত, ওটা শূণ্য, এটা শূণ্য, শূণ্য থেকে শূণ্য নির্গত হচ্ছে আর শূণ্য থেকে শূণ্য গেলে শূণ্যই পড়ে থাকছে। অবশ্য প্রকৃতির একটা জায়গায় এর প্রয়োগ আমি দেখতে পাই জীবকোষ বিভাজনের সময়। একটা কোষ ভেঙ্গে যখন দুটো একই রকমের কোষে পরিণত হয় তখন একটা কোষকে পূর্ণ ধরলে, পূর্ণ থেকে পূর্ণ এসেও পূর্ণই পড়ে থাকল। ঋষিরা হয়ত লম্ফ জ্বালানোর সময় এটা আবিষ্কার করেছিল।
সবাইকে হাসতে দেখে আমি চুপ হয়ে গেলাম। তখন ওঁদের মধ্যে আর একজন আমায় আবার জিজ্ঞাসা করল
– এসব কথা ছাড়ুন। আচ্ছা, এই যে আপনাকে আমি দেখছি, একজন ভারতীয়, ছোটোখাটো চেহারার, চশমাপড়া উদাস দৃষ্টি যেন কোথায় হারিয়ে আছে, ভদ্রলোকটাকে। এও কি সত্য নয়?
– মানুষের চোখদুটো যে কি দ্যাখে তা কেউ জানে না। আপনি যা দেখছেন, অর্থাৎ এই কালো, বোকার মতন উঁচু দাঁতের হাঁ করা লোকটা (আমার ঠাকুমাকে বা মা-কে আমার নামে এভাবে কেউ বললে হয়ত তাঁর আর এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকা হ’ত না) সেটা আপনার জ্ঞানের প্রেক্ষণ। আমার দিকে তাকাবার ফলে আপনার রেটিনাতে যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তাকে ক্রমাগত অনুবাদ করে চলেছে আপনার জ্ঞান। আপনার অজান্তে ছোটোবেলা থেকে আপনাকে যা শেখানো হয়েছে, তা মনের মধ্যে শব্দ দিয়ে প্রকাশ করে যোগাযোগ সৃষ্টি করে নামকরণ হয়ে চলেছে। এই নামকরণের প্রক্রিয়া যদি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে যে কি দেখা যায় তা বলার যে কেউ থাকে না। ওঁদের মধ্যে চালাক ধরণের একজন তখন বলল
– কিছুই হয়ত দেখা যায় না কারণ প্রমাণ তো করা যাবে না।
আমি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আর একটা প্রশ্ন আসতেই আমার মুখটা বন্ধ হয়ে গেল।
– তাহলে আমাদের মধ্যে কেন এত প্রয়াস, জিজ্ঞাসা, জ্ঞান পিপাসা?
– মানুষ তাঁর বুদ্ধি দিয়ে দেখল প্রকৃতির চালচলনের মধ্যে একটা নিয়ম আছে, লজিক আছে, কনসিস্টেন্সি আছে। সঙ্গে সঙ্গে সে নিয়মগুলো প্রকৃতির উপরই প্রয়োগ করার চেষ্টা করল, সমর্থ হ’ল, গড়ে উঠতে লাগলো সভ্যতা। যতই গড়ে, ততই নতুন নতুন কায়দা শেখে, চলল প্রগতি। মানুষ হয়ে উঠল অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী। এখন নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন কি অসম্ভব সব কাজ মানুষের পক্ষে করা সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। কিন্তু মানুষের দুঃখ, হতাশা, বেদনার কোনো উপশম হয়নি। মানুষের কারিগরি জ্ঞান এবং প্রযুক্তির মূলে হ’ল প্রকৃতির নিয়মের উপর গভীর বিশ্বাস। প্রকৃতির নিয়মে আপনার কোনো সন্দেহ নেই, যদি সন্দেহ থাকত তাহলে আপনি কোনদিন প্লেনে চড়তেন না, ওষুধ খেতেন না এবং আরো বহু রকমের কাজ করতে সাহস পেতেন না। এর উপর আপনার পরিপূর্ণ বিশ্বাস। এর উপর বিচার করেন না, পুরোপুরি মেনে নিয়েছেন। কখনই বলেন না কেন সৌরমন্ডলে আমার জন্ম হ’ল? কেন আমি অন্য গ্যালাক্সিতে জন্মালাম না? অথচ সেই আপনি আপনার দিকে তাকালেন, আপনার সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের দিকে তাকালেন, আপনার জীবনকে তুলনামূলকভাবে দেখলেন, তখন ভালো-মন্দের বিচার শুরু হয়ে গেল। আপনি আপনার অবস্থাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। আপনার গুণাবলী আপনার পছন্দ হয় না, নিজে যা সেটাকে সবসময় পরিবর্তিত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন – অন্য কারোর মতন হওয়ার প্রচেষ্টা, মরীচিকার পেছনে ছোটার মতন – একথা আপনি কিছুতেই উপলব্ধি করতে পারছেন না। কারণ বিচার ছাড়া আপনার অস্তিত্ব লুপ্তপ্রায় – এটা বোঝা আপনার স্বার্থের প্রতিকূল। আবার ধরুন আমি কুৎসিত আর আপনি সুন্দরী এই দুটো ঘটনার মধ্যে এবং পশ্চাতে আমাদের কি কোনো হাত আছে? নেই। অতএব এ ব্যাপারে আমার হতাশার এবং আপনার গর্বের কোন কারণ থাকা উচিত নয়। তাই না? কিন্তু এসব কথা জানার পরেও ওই সমস্ত ভাবনা আমাদের ভেতর থেকে যায় না। আপনি হয়ত আরও অবাক হয়ে যাবেন এই কুৎসিত-সুন্দরের ধারণা কত আপেক্ষিক তা জেনে। মহাভারতের গল্প শুনেছেন নিশ্চই, যুবক দেবব্রতের নাম শুনলে হৃদয়ের গোপন গভীরে কম্পন জাগত না এমন তরুণী সে যুগে ছিলনা। অথচ পিটার ব্রুকসের মহাভারতে ভীষ্মকে এমন দেখতে যে আমার স্ত্রী টিভি বন্ধ করে আর মহাভারতই দেখল না। ছোটোবেলায় দাদুর শাঁকচুন্নির বর্ণনার মতন হাড় জিরজিরে মেয়েদের দিকে আমাদের ওখানকার বাঘা বাঘা লোকেরা দেখি হাবার মতন তাকিয়ে থাকে, যেন বহুদিনের উপবাসী। অতএব এই যে দ্বন্দ্ব একদিকে প্রকৃতির নিয়মে অসাধারণ সামঞ্জস্য আর অন্যদিকে সামাজিক নিয়মগুলো তালগোল পাকানো একটা কিম্ভুত কিমাকার জিনিস। এই দুয়ের মধ্যে মানুষ ভারসাম্য আনতে পারছে না। হয়ত আরও কিছু জানলে বা আরও কিছু করলে দুঃখমোচন হবে। বুদ্ধি এবং আশা এমনভাবে মানুষের মধ্যে আরোপ হয়ে আছে যে অক্ষমতার কোন স্থান সেখানে নেই। দু-হাত উপরে ছুঁড়ে দিলে হারিয়ে যাওয়ার ভয়। যতদিন আত্মবোধ ততদিন প্রশ্ন ও প্রয়াস। মানুষের মধ্যে যে ভুল চালাকিটা বিপরীতার্থক নীতির মতন কাজ করে চলেছে তা বোঝা মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার মতন। তাই আমরা এসব দেখেও না দেখার ভান করে যে যাঁর ব্যাস্ততা নিয়ে বেঁচে থাকি।
– কিন্তু সমাজে থাকতে গেলে কিছুতো করতে হবে, জানতে হবে সত্য কি। ভালো-মন্দ বোঝা দরকার তাই না? এ ব্যাপারে কিছু বলুন।
– আমি কখনোই বলছি না কোন্টা ভালো, কোন্টা খারাপ। আপনি কি করবেন আর কি করবেন না এটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যাপার। আপনি অবশ্যই সত্য অনুসন্ধান করবেন। আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই যে যদি আপনি আগাগোড়া সততা ও সাহসের সঙ্গে অনুসন্ধান চালিয়ে যান তাহলে দেখতে পাবেন যে আপনি কত অসহায়। আপনাকে অন্যের জ্ঞানের উপর কতখানি নির্ভরশীল হতে হবে। কোন্টা প্রকৃতি আর কোন্টা মায়া এটা বিচার করার জন্য আপনার ভেতর একটা কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দু থাকতে হবে। আর কাঠামো পুরোপুরি সামাজিক সংযোজন। আপনি, আপনি বলতে যা মনে করছেন তাতে আপনার কিছুই নেই, বাইরের লোকজন আপনার মধ্যে ওসব জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে। আর সেই অস্তিত্বহীন ‘আপনি’-র পরিপ্রেক্ষিতে সমানে বিচার করে চলেছেন। আজ ভাবছেন এটা ঠিক, কাল ভাবছেন ওটা ঠিক, আর এভাবে বিচার করতে করতেই একদিন এই দেহযন্ত্রটা অকেজো হয়ে যাবে। তাঁর কিছুক্ষণ আগে কেন্দ্রবিন্দুও অদৃশ্য হবে। এই করুণ পরিণতির কোনো অন্যথা নেই। একজন যা এ অবস্থায় করতে পারে তা হ’ল তাঁর যুবক (যুবতী) বয়সেই নিজের কাছে প্রাণের সমস্ত সততা দিয়ে এ প্রশ্ন করা উচিত – সে কি চায়? আর তার উপর নির্ভর করে সে কি করবে এবং কি পাবে!
ইতিমধ্যে লক্ষ্য করলাম তাঁরা সবাই গোল করে চতুর্দিকে বসে পড়েছে, আর কেউ কোন প্রশ্ন করছে না। সবাই নিস্তব্ধ! শুধু নদীর ঢেউগুলো ঘাটের উপর ছলাৎ ছলাৎ করে ভেঙ্গে পড়ছে। সেই শব্দে আমার রক্তে নেশা লেগে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলাম। একজন আমায় তখন বলল যে আমি যদি ইচ্ছা করি তাহলে আমাকে তাঁদের গুরুদেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে। এবার বুঝলাম তাঁরা আমায় এসব প্রশ্ন কেন করছিল। সবাই এক বিশেষ মতামত সম্পন্ন দলের লোকজন। তাঁদের আধ্যাত্মিক গুরুর নাম হ’ল ‘শিবানন্দ রাও’। উপস্থিত ছেলেমেয়েদের মধ্যে একজন এই রাজবাড়ীর প্রথম রাজার সরাসরি বংশধর। তাঁদের গুরু নাকি এক অসাধারণ যোগী, অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী। আমাকে তাঁদের সবার খুব ভালো লেগেছে, আরও বলল যে, সাধারণ লোকজন তাঁদের গুরুর সাথে দেখা করার কোনো সুযোগ পায় না। অবশ্য আমি যদি ইচ্ছা করি, তাহলে এমন কি একা একাও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি।
আমি নম্রভাবে বললাম আপাতত আমার সেরকম কোনো ইচ্ছা নেই। সবাই প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিল। নদীর ওপাড়ে এক গ্রামে গুরুদেব উঠেছেন, সেখানে যাবে।
সমস্ত রাজবাড়ীতে আমি তখন একা। আমার সাথে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে এই জনমানবশূণ্য রাজপ্রাসাদ। পরাক্রান্ত দিবাকর তখন জীবনের শেষ লগ্নে, পরপারের সবাইকে ঘুম ভাঙ্গানোর তাগাদায় আমার নামটার মতন তড়িঘড়ি ডুব মারার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছে। এই রোমাঞ্চকর পরিবেশে স্রোতস্বিনী ততক্ষণে এক মোহিনীর রূপ ধারণ করেছে। কমলা রং এর বিশাল সূর্যের প্রতিবিম্বকে এলিয়ে দুলিয়ে ঐশ্বর্যমন্ডিত হয়ে আমাকে রাঙিয়ে দিয়েছে। সূর্যের নরম আলো যেন গায়ে কুসুম ছড়িয়ে দিচ্ছে। পুলকে শরীর অস্থির, চোখে নেশার ঘোর। আর বসে থাকতে পারলাম না। শূণ্য প্রাসাদের বারান্দা ধরে মন্ত্রমুগ্ধের মত হাঁটতে লাগলাম। নদীর সারা অঙ্গে চুমু দিয়ে উড়ে আসা পড়ন্ত বেলার ভেজা হাওয়া মৃত ঝরা পাতাগুলোকে নিয়ে খেলা করতে করতে হঠাৎ আমার মুখে, বুকে আছড়ে পড়ল। যেন আমাকে বলছে – দেখ ওই পাতাগুলোকে, ওরা মৃত অথচ উজ্জ্বল, রঙ্গীন এবং অপূর্ব সুন্দর। জানো, ঝরে পড়ার ঠিক আগে ওদের সৌন্দর্য যেন গাছে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হ’ল ওরা এখন গভীর ধ্যান সমাধিস্থ। আবার বসন্তে চোখ খুলবে। দেখতে দেখতে বারান্দার শেষপ্রান্তে এসে হাজির হলাম, ছোট একটা ঘরের সামনে। দরজা খোলা, মনে হ’ল পূজার ঘর। ভালো করে নজর পড়তে বোঝা গেল ঘরের মধ্যে কোনো একজন লোক নড়াচড়া করছে। আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। দেখি একজন আধশোয়া অবস্থায় বসে আছে। খালি পা, মালকোঁচা দিয়ে ধবধবে সাদা ধুতি পড়া, খালি গা, মুখের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলাম, এ যে হাতির মাথা! আরও কাছে গিয়ে ভালো করে তাকালাম গোলাপী রঙের শরীর, হাত-পা একটু মেয়েলি ধাঁচের, সত্যিই অনিন্দ্যসুন্দর। আমাকে দেখে ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেছে, বিনয়ের সঙ্গে মেয়েলি গলায় মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে বলল,-“আমি গণেশ, আমি গণেশ, সত্যি বলছি আমি গণেশ”। অবাক হয়ে গেলাম তাঁর ব্যাবহার দেখে, মনে হ’ল লজ্জায় যেন মাথা তুলতে পারছে না। আমার ভেতর তখন আনন্দের জোয়ার বয়ে চলেছে। দারুন আদর করতে ইচ্ছে হ’ল। কোনরকম অনুমতি না নিয়েই হাতে পায়ে অনেকগুলো লম্বা— চুমু খেলাম। তাতে আরও লজ্জা পেয়ে কাঁচুমাচু হয়ে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলতে লাগল – “আমি গণেশ, আমি গণেশ, বিশ্বাস করুন আমি সত্যিই গণেশ”।
রাজপ্রাসাদ ছেড়ে নদীর তীরে চলে এলাম। একটু দক্ষিণে দেখলাম একটা সেতু। ওপাড়ে যাব ঠিক করলাম। সেতুর উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যখন প্রায় নদীর মাঝখানে এসে পড়েছি তখন একটু থামলাম। রাজবাড়ীর দিকে ঘুরে তাকালাম। অপূর্ব লাগছিল দেখতে। মনে হ’ল শত শত বছর ধরে কালের স্রোতকে উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে শুধু এমন কয়েকটা সূর্যাস্ত দেখার জন্য। সার্থক অপেক্ষা! স্থপতিকে মাথার উষ্ণীষ খুলে অভিনন্দন জানাতে ইচ্ছে হ’ল। এপাড়ে এসে হঠাৎ মনে পড়ল, আরে, ইউজী কৃষ্ণমূর্তি তো এখানেই থাকেন, তাড়াতাড়ি ওঁনার কুটীরের সামনে এসে দরজায় টোকা দিলাম। ইউজী দরজা খুলে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন কখন আসা হ’ল, কেন আসা হ’ল ইত্যাদি ইত্যাদি যতসব অদরকারী প্রশ্ন। আমি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম শিবানন্দ রাও বলে কোন যোগীর নাম শুনেছেন কখনো। নদীর এপাড়েই নাকি কোথাও উঠেছেন, অনেক চ্যালা-চামুন্ডা, অদ্ভুত সব ক্ষমতার অধিকারী। ভাবছি একবার সাক্ষাৎ করে আসি। বুড়ো মাথা নেড়ে বললেন ছোটবেলায় হিমালয়ে যাঁর কাছে যোগাসন শিখতাম তাঁর নাম ছিল শিবানন্দ সরস্বতী, কিন্তু রাও বলে কাউকে চিনি না, তবে একটা কথা শুনে রাখো এসব ক্ষমতা ইন্দ্রজাল কমিকের গল্পের মতন, কোনো কাজে লাগে না। শুধু লোককে বোকা বানানো যায়। এইসব বলতে বলতে আমরা ঘর থেকে বেড়িয়ে এসে একটা বটগাছের নীচে বেদীতে বসলাম।
চুপচাপ নদীর দিকে তাকিয়ে থেকে বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল। বুড়ো আমায় উত্তর দিকের একটা বাড়ী দেখিয়ে বললেন, ঐ বাড়ীতে আজ অনেক লোকের যাতায়াত লক্ষ্য করলাম, হয়ত ওখানেই শিবানন্দ রাও-র চ্যালা-চামুন্ডারা জমায়েত হয়েছে। বাড়ীটা আমরা যেখানে বসেছিলাম তাঁর থেকে অনেকটা নীচুতে। আরও কিছুক্ষণ পরে মনে হ’ল সমস্ত লোকজন যাঁরা যাঁরা জমায়েত হয়েছিল তাঁরা সবাই যে যাঁর নিজের নিজের গন্তব্যস্থলে চলে গিয়েছে। আর কোনরকম গতিবিধি লক্ষ্য করা গেল না। আমরা আবার অন্যমনস্ক হয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে রইলাম। মাঝেমাঝে ইউজীর সঙ্গে একটু আধটু কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময় লক্ষ্য করলাম একজন লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। ভদ্রলোকের মাথায় একটা মূর্তি, সেই নীচের বাড়ী থেকে এসে, সিঁড়ি বেয়ে আমাদের দিকে উঠে আসছে। আর একটু কাছে আসতে বোঝা গেল মাথার মূর্তিটা গণেশের। আমাদের খুব কাছাকাছি এসে চোখ দিয়ে অভিবাদন করল, কারণ ওঁনার দুটো হাতই ব্যাস্ত, মূর্তির পা-দুটো ধরে আছে। আমাদের লক্ষ্য করে বলল, তাঁর গুরুদেব শিবানন্দ রাও আজ ওপাড়ের রাজবাড়ীতে গণেশের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবেন, তাই এই মূর্তি নিয়ে সেখানে যাচ্ছে। আমি বললাম, তা বেশ, আপনি সেই রাজবাড়ীতে এই মূর্তি নিয়ে শীঘ্রই চলে যান কিন্তু কাজের কাজ আগেই হয়ে গেছে। ভদ্রলোক আমার কথা কিছুই বুঝলো না। সেতুর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, ওইযে, আমার গুরুদেব আসছেন, আমি এগিয়ে যাই।
বিশাল চেহারার ভদ্রলোকটি সিঁড়ি বেয়ে আমাদের দিকে উঠে এলেন। গেরুয়া আরা লালের মাঝামাঝি একটা রঙের ধুতি পরনে। কাছে আসতেই ইউজী অত্যন্ত ভদ্রভাবে উঠে গিয়ে সম্বর্ধনা জানিয়ে বললেন, নমস্কার। আমি শিবানন্দজীকে নমস্কার জানিয়ে বললাম, এঁনার নাম ইউজী কৃষ্ণমূর্তি। নাম শুনে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে ইউজীকে প্রণাম জানালেন। তারপর হঠাৎ আমার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,
– “আপনি কি সব্যসাচী গুহ?”
আমি প্রায় গাছ থেকে পড়ার মত থতমত হয়ে বললাম,
– “আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্ত আপনাকে আমি কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না?” উনি অমায়িক হাসি দিয়ে বন্ধুর মত ভাব দেখিয়ে বললেন,
– “ভক্তদের কাছে আপনার অনেক গুণগান শুনলাম। ওপাড়ে আজ গুরু প্রতিষ্ঠা করব, এক স্বনামধন্য শিষ্যের বাড়ীতে, সিদ্ধিদাতা বিনায়কের, আসুন না আমার সাথে গুরুপূজা দেখবেন”। মনে মনে ভাবলাম ওপাড়ে যা দেখে এসেছি তা যদি বলি তাহলে হয়ত বিপত্তি ঘটতে পারে। তাই চুপচাপ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমাকে কোনরকম উচ্চবাচ্য করতে না দেখে ইউজী নম্রভাবে বললেন,
– “দেখছেন না গুহর পা-দুটো কেমন স্থির হয়ে আছে, আপনি বরং এগিয়ে যান। হাতে আর বেশী সময় থাকবে না”।
শিবানন্দ রাও একটু এগিয়ে গিয়ে হাতদুটো আকাশের দিকে উঠিয়ে প্রণামের ভঙ্গিতে একপদাসনে দাঁড়িয়ে ছবির মতন নিশ্চল হয়ে রইলেন। আমি ইউজীর দিকে তাকিয়ে বললাম,
– “চেহারা দেখেছেন? সাতফুট লম্বা”।
ইউজী হাসতে হাসতে বললেন,
– “বয়, হি ইজ হিউজ!”
যোগী শিবানন্দ রাও’র চোখদুটো বন্ধ, গভীর মনোযোগ দিয়ে প্রাণায়াম করছেন। এত দীর্ঘস্থায়ী কুম্ভক করতে কাউকে এর আগে কখনও দেখি নি। মনে হচ্ছে আমি যেন স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন দেখছি। তাঁর দেহের ঘনত্ব ধীরে ধীরে কমতে লাগল, শরীরের ভিতর দিয়ে আমি ওঁনার পেছনে সেতুর অংশটা আবছা আবছা দেখতে পাচ্ছি। তিনি প্রায় স্বচ্ছ হয়ে এসেছেন – এবার অদৃশ্য! অথচ আমি যেন সব দেখতে পাচ্ছি – কেউ আমায় মনে করিয়ে দিল একে বলে দিব্যদৃষ্টি – দেখলাম ওঁনার সূক্ষ্মদেহটা। অন্য এক জায়গায় চলে যাচ্ছে, নদীর উপর দিয়ে – ওপাড়ে সেই রাজপ্রাসাদের ছাদে। সেখানে বিরাট সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে, প্রচুর লোকজনের জমায়েত হয়েছে। ছোটখাটো একটা বেদীর উপর সুন্দর একটা আসন পাতা আছে। সূক্ষ্মদেহটা আসনের উপর উপবেশন করলো, শিবানন্দ রাওজীর স্থূলদেহ সূক্ষ্মদেহের চারিধারে ধীরে ধীরে প্রকাশ হতে লাগল। আগে যখন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল তখন যদি কেউ ভিডিও করে রাখত, তাহলে রিভার্স অ্যাকশন রিপ্লে করলে যেমন দেখাত ঠিক সেরকম।
রাজবাড়ীর ছাদে কাঁসর ঘণ্টা ও শাঁখ বাজছে, ভদ্রলোকের নামে জয়ধ্বনি হচ্ছে,- “শিবানন্দজী কি জ্যায়……”। মহিলা ভক্তেরা আবেগে হাউ হাউ করে কান্না জুড়ে বসেছে। আমি আর কি করি, দিব্যদৃষ্টির স্যুইচটা বন্ধ করে দিলাম, চোখের সামনে সেতুটা দেখলাম পরিষ্কারভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ঘাড় ফিরিয়ে ইউজীর দিকে তাকালাম, জিজ্ঞাসা করলাম, -“এসব কি দেখছি?” ইউজী আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়েই বললেন, – “এসব ভেবে সময় নষ্ট করা আর ঠিক হবে না। চলো, আমাদের অনেক দূরে যেতে হবে”। মনে মনে ভাবলাম এক কঠিন বুড়োর পাল্লায় পড়েছি……… স্বপ্ন শেষ।
ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে কফি বানালাম। কফি খেতে খেতে নিজের হাত পায়ের দিকে তাকালাম। একটু চিমটি কাটলাম, না জেগেই আছি, কারণ বলা মুশকিল কোন্ অবস্থার নাম স্বপন আর কোন্ অবস্থার নাম জাগরণ। এবার ভাবতে লাগলাম, আমার মাথার মধ্যে কত রকমের মালমশলা লুকিয়ে আছে, ওয়াইল্ড ইমাজিনেশন। নয়ত এরকম একটা জীবন্ত স্বপ্ন! হয়ত মাথাটা সত্যি সত্যি গেছে! জ্ঞান দিয়ে বোধহয় এ সমস্ত কুসংস্কার মুছে ফেলা যায় না। এ কি আর সামান্য কয়েকদিনের জমা হওয়া জিনিস। সেই ছোটবেলা থেকে শুরু হয়েছিল। মনটা হু হু করে ছুটতে ছুটতে রবীন্দ্রনগরে পৌঁছে গেল।
সেই সময় ঠাকুমার কোলে শুয়ে মনসামঙ্গল কাব্য শুনতাম। ঠাকুমা আবার আদর করে বলত, “ও পিদ্দীপ! আমার সাথে গলা মেলা ………… বেহুলা চলে, চলে রে গম্ভীর জলে………। তারপর দেখতাম মা-কে। ছোট্ট ঠাকুরের আসনের সামনে বসে প্রদীপের কম্পিত শিখার আলো-আঁধারে একটা পুরনো ছেঁড়াফোড়া বইয়ের দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে দুলে দুলে পড়ত ………… দোল পূর্ণিমা নিশি নির্মল আকাশ, ধীরে ধীরে বহিতেছে মলয় বাতাস …………। আর একটু বড় হতেই আমার শান্ত-সমাহিত অন্তর্মুখী ভাবসাব মা-বাবার পছন্দ হ’ল না, দিল পাঠিয়ে মায়ের গুরুদেবের আশ্রমে। সেখানে জোর জবরদস্তি করে রোজ ভোর পাঁচটায় ধুতি পরে প্রার্থণা করতে বাধ্য করেছিল। কুশাসনে বসে ধ্যান করতে হয়েছিল, গীতা মুখস্ত করতে হয়েছিল। কত রকমের সাধূ-সন্ন্যাসী দেখতাম, পঞ্চমুন্ডী আসন, মৌনীবাবার আশ্রম, নানারকম অলৌকিক গল্পকাহিনী। আর একটু বড় হলাম, দেখি বাবুর জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর অগাধ বিশ্বাস। বই পড়ে হাত দেখা শিখলাম। দেখতাম স্নানের পর বাবু চোখ বুজে সূর্যস্তব করত, -“ওঁ জবাকুসুম শঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্ ধ্বন্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোস্মি দিবাকরম্”। তাঁর দেখাদেখি আমিও সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চারুধারে যে সমস্ত চ্যালা-চামুন্ডা ঘুরঘুর করছে অহর্নিশি, নয় নয় করে সবার গুণাবলী গাঁথা মুখস্থ করে ফেললাম। হ’ল বন্ধুর পৈতা, আমি কায়েতের ছেলে, আমাকে বলবে না কি মন্ত্র শিখেছে। ঠিক বই খুঁজে মন্তর মুখস্থ করে বন্ধুকে রোজ শোনাতাম। এই সবকিছু অনেক কসরৎ চেষ্টা চরিতার্থ করে কুসংস্কার ভেবে হয়ত বা মুছে ফেলতে পারলাম, কিন্তু জেনেটিক্স বলছে বংশ পরম্পরায় নাকি অনেক কিছু চলে আসে। তা যদি সত্যি হয় তাহলে তো আমার করার কিছুই নেই, আমি অসহায় – কত প্রজন্ম ধরে এসব জ্বলন্ত বিশ্বাস, পূজা-পার্বন যে রক্তে মিশেছে কে জানে। জন্মগত রোগ হয়ত কোনো চিকিৎসা নেই।
ফোনের ঝনঝনাৎকার আমাকে নিউজার্সিতে ফিরতে বাধ্য করল। উঠে গিয়ে অনিচ্ছাসত্বেও ফোনটা তুললাম। লক্ষ্মী সুইজারল্যান্ড থেকে ফোন করেছে – সুইজারল্যান্ড যেন কৈলাশ পর্বত, কিছুতেই বোধগম্য হয় না …………। খাওয়া-দাওয়া, কাজকর্মে্ শরীরস্বাস্থ্যের রুটিন চেকআপের পর বলল,
-“শোনো, একটা খুব ভালো খবর আছে! ইউজী শিল্পা-সুমেধার পড়াশোনার জন্য প্রচুর টাকাপয়সা ওঁদের নামে ব্যাঙ্কে জমা করেছে”।
আমি বললাম,
-“তাহলে আমি এবার নিশ্চিন্তে অবসর গ্রহণ করতে পারি। বাদবাকী জীবনটা গাছতলায় বসে লোকজনকে আধ্যাত্মিকতার কথা শুনিয়ে কাটিয়ে দিতে পারি”।
সহধর্মিনী, যিনি একসাথে মানবিক ধর্ম প্রাণ দিয়ে তুলে ধরবেন, তাঁর আমার এই পরাজ্ঞানের কথাটা একটুও পছন্দ হ’ল না। বলল
–“চেষ্টা করে দ্যাখো। ঠান্ডা লেগে যখন হাঁপানীতে ধরবে তখন চীৎকার করলেও আসব না”।
আমি ওঁকে একটু জব্দ করার জন্য বললাম,
-“দ্যাখো এসব রোগ, প্রকৃতি আমার ডি এন এ তে ইলেক্ট্রনের হাতুরী-বাটালী দিয়ে খোদাই করে দিয়েছে। সেই ভয়েতেই তো হিমালয়ে যাওয়া হ’ল না, তপস্যা করা হ’ল না, উলটে তোমায় বিয়ে করে বসলাম”।
ওঁ আমার লেসারের বাণটা আয়না দিয়ে আমার দিকেই ঘুরিয়ে দিল। বলে উঠল,
– “পূর্বজন্মে প্রচুর ভালো কাজ করে, অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্মফল নিয়ে এবং সঞ্চিত ভাগ্যের সুবাদে সৎ, ধার্মিক মা-বাবার মাধ্যমে এই পৃথিবীতে এসেছিলে। তাই পরমপিতা করুণা ভরে তোমায় আমার কাছে পাঠিয়েছিল। এখন আর ওসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনার কোন দরকার নেই। মনযোগ দিয়ে কাজকর্ম কর”।
আমি হতাশ হয়ে ভাবলাম এ বিচার কে করবে? কাকে কে উদ্ধার করে? বললাম,
-“তুমি যে ভাগ্যবতী তাতে কোন সন্দেহ নেই”।
এবার হয়ত একটু খুশী হ’ল। কথাবার্তা প্রায় শেষ। শিল্পা-সুমেধা সারাদিন খেলে বেড়াচ্ছে। সুনীল শেঠ্টির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। আরও সব লোকজনের সঙ্গে এখানে ওখানে বেড়াতে যাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। ফোনটা রাখার ঠিক আগে আমায় লক্ষ্মী বলল,
– “ও বলতে ভুলে গেছি আজ বিনায়ক চতুর্থী”।
আমি ফোনটা রেখে সেই যে সোফায় বসলাম – বাক্যহীন। সম্বিৎ ফিরতে ফিরতে দেখি অফিসের অনেক দেরী হয়ে গেছে।
কি হাসি থামল? মা-কে পড়াস। আর সবাই ভালো থাকিস।
